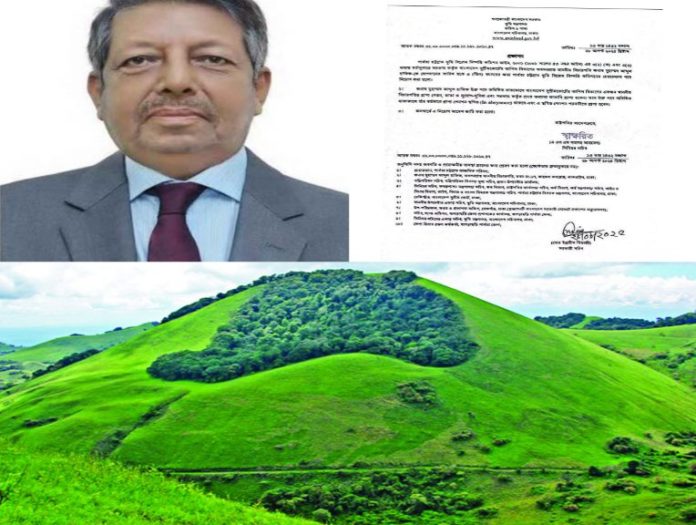হান্নান সরকার | পার্বত্য চট্টগ্রাম
ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুসারে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে, স্বাক্ষরিত
(এ এস এম সালেহ আহমেদ) সিনিয়র সচিব, স্মারক নম্বরঃ ৩১.০০,০০০০,০৪৯.১১.১২৮.২০১০,৪৭ জারি হওয়া এই প্রজ্ঞাপন আবারও নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বহুমাত্রিক ভূমি-রাজনীতি ও জাতিগত দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে। এই নিয়োগ কেবল প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অংশ নয়, বরং এ অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক বাস্তবতায় গভীর প্রভাব বিস্তারকারী এক রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ।
উপজাতিরা দাবি করে যে পার্বত্য অঞ্চলের সমগ্র ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি তথা তাদের প্রথাগত মালিকানার অধীনে, যেখানে কোনো আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র বা খাজনা দাখিলার প্রয়োজন নেই—শুধুমাত্র বংশপরম্পরায় ভোগদখলের সূত্রে। এদিকে, সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে প্রায় চার লক্ষ বাঙালিকে সমতল থেকে পুনর্বাসিত করেছে, যাদেরকে সরকারি খাস ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এই বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় জেলা প্রশাসকরা হেডম্যানদের রিপোর্ট গ্রহণ না করায় উপজাতিরা অভিযোগ তোলে যে এটি শাসনবিধির লঙ্ঘন। কিন্তু দেশের প্রচলিত ভূমি আইন অনুসারে এই দাবি অযৌক্তিক, কারণ পার্বত্য অঞ্চলের শাসনবিধি দেশের সংবিধান ও আইনের সাথে সংঘাতপূর্ণ।
২০০১ সালের ৫৩ নম্বর আইনের আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘদিনের ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন করা। কিন্তু আইনটির নানা ধারা শুরু থেকেই বিতর্কিত ছিল। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী প্রথাগত শাসনবিধির আওতায় সমগ্র পার্বত্য ভূমির ওপর মালিকানা দাবি করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কাছে প্রমাণসাপেক্ষ দলিল নেই। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের পুনর্বাসন কার্যক্রমের বাঙালিরা সরকার থেকে ভূমির মালিকানার কাগজপত্র পেয়েছে। এখানেই সংঘাতের সূচনা, একদিকে প্রথাগত দাবি, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বন্দোবস্তের আইন।
বিতর্কিত আইন ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর আশঙ্কা: আইন অনুযায়ী কমিশনের রায় চূড়ান্ত এবং এর বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করার সুযোগ নেই। এ বিষয়টিই সবচেয়ে বড় আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে স্থানীয় বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে। তারা মনে করেন, এই কমিশন কার্যকর হলে তা একতরফাভাবে উপজাতিদের পক্ষে যাবে এবং বাঙালিরা তাদের আইনি মালিকানাধীন জমি থেকে উচ্ছেদ হবে।
তাদের অভিযোগ— কমিশনে উপজাতি সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, বাঙালি সদস্য রাখা হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী উপজাতিরা ২২ হাজার অভিযোগ কমিশনে জমা দিয়েছে, যার রায় হলে বাঙালিরা ভূমি হারাবে। আইনটি দেশের প্রচলিত ভূমি আইনের পরিপন্থী।
২০০১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বাঙালিরা এ আইনের সংশোধন দাবি করে এসেছে, কিন্তু কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে কমিশন কার্যত অকার্যকর থেকেছে।
হঠাৎ নিয়োগ: প্রেক্ষাপট ও প্রশ্ন! কমিশনের পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দীর্ঘদিন এই পদ শূন্য ছিল। এ সময়ে কোনো কার্যক্রমই পরিচালিত হয়নি। কিন্তু গত ১৮ আগস্ট “পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন” নামে একটি অখ্যাত সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শরিফুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভা করে ভূমি কমিশন সক্রিয় করার দাবি তোলে। মাত্র দশ দিন পরেই গত ২৮ আগস্ট ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি হয়। এই সময়কাল অনেকের কাছে কাকতালীয় মনে হলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিষয়টিকে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখছেন।
বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ: ব্যক্তিগত পর্যালোচনা: ১৯৫৭ সালে জন্ম নেওয়া বিচারপতি আব্দুল হাফিজের বিচারিক জীবন সমৃদ্ধ ও দীর্ঘ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি জজ কোর্ট, হাইকোর্ট হয়ে আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সুনামকে সামনে রেখে এই নিয়োগকে সরকার যুক্তিযুক্ত বললেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এত জটিল ও বিতর্কিত একটি প্রতিষ্ঠানে তাঁর ভূমিকা কি কার্যকর হতে পারবে? নাকি তিনিও পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানদের মতো প্রশাসনিক জটিলতা ও রাজনৈতিক চাপের কারণে কোনো বাস্তব পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হবেন?
পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনীতি: পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি প্রশ্ন শুধু আইনি নয়, বরং তা ভূ-রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত দিক থেকেও অতি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৯ সালে বাঙালি পুনর্বাসনের পর থেকে এ অঞ্চলের জনসংখ্যাগত গঠন পাল্টে গেছে। এখন যে কোনো ভূমি কমিশনের সিদ্ধান্ত সরাসরি জনসংখ্যার ভারসাম্য, রাজনৈতিক প্রভাব ও সামগ্রিক নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলবে। স্থানীয় বাঙালিরা বিশ্বাস করেন, ভূমি কমিশন সক্রিয় হলে এটি তাদের অস্তিত্ব সংকটকে ত্বরান্বিত করবে। অন্যদিকে উপজাতি গোষ্ঠীগুলো দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক মহলের সহায়তায় প্রথাগত অধিকারের দাবিতে সোচ্চার রয়েছে।
আইনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব: প্রথাগত অধিকার বনাম রাষ্ট্রীয় আইন: উপজাতিদের দাবি বনাম সরকারের বন্দোবস্ত আইন। চূড়ান্ত রায় বনাম ন্যায়বিচারের অধিকার: কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল অযোগ্যতা। সদস্য নির্বাচন বনাম জাতিগত ভারসাম্য: কমিশনে বাঙালিদের কোনো প্রতিনিধি না থাকা।
এই দ্বন্দ্বগুলো সমাধান না হলে কমিশন কার্যকর হওয়া মানেই হবে নতুন করে সংঘাতের উন্মেষ।
আশঙ্কা ও সম্ভাবনা: একদিকে রয়েছে গভীর আশঙ্কা, বাঙালিদের উচ্ছেদ, আইনের অপপ্রয়োগ, আন্তর্জাতিক চাপ ও নিরাপত্তাহীনতা। অন্যদিকে, সঠিকভাবে পরিচালিত হলে ভূমি কমিশন দীর্ঘদিনের বিরোধ নিষ্পত্তি করে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এজন্য প্রয়োজন আইনের সংস্কার ও ন্যায়সঙ্গত সংশোধন,
উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, আপিল করার অধিকার দেওয়া, আন্তর্জাতিক নয়, বরং রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সকল ভূমি পরিমাপ করে মালিকানার বৈধ কাগজপত্র অনুযায়ী প্রকৃত প্রাপ্তদের ভূমি বুঝিয়ে দেওয়ার পর অবশিষ্ট ভূমি দাবিকারীদের বুঝিয়ে দেওয়া।
বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজের নিয়োগ নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু কেবল একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ চেয়ারম্যান নিয়োগ দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। কমিশনের মৌলিক আইনি কাঠামো যদি বিতর্কিত ও একতরফা থাকে, তবে এই নিয়োগও অচলাবস্থার আরেকটি অধ্যায় হয়ে থাকবে।
পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা কোনো একক গোষ্ঠীর দাবিতে সমাধানযোগ্য নয়। এটি সমাধান করতে হলে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় আইনের আলোকে সমগ্র ভূমি পরিমাপ, ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং সর্বস্তরের জনগণের আস্থা। অন্যথায় এই নিয়োগও হয়ে উঠবে কেবল আরেকটি রাজনৈতিক কৌশল, যা পাহাড়ে শান্তির বদলে নতুন সংকটের জন্ম দেবে।